রাজনীতি সবসময়ই ক্ষমতার চারপাশে ঘোরে, ক্ষমতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের ধারণাটি তৈরি হয়েছিল ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ এবং এর আইনি ও নৈতিক প্রয়োগকে সক্ষম করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হলো নাগরিক এবং তাদের নেতারা কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গঠনমূলক এবং নীতিগতভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন, তা নির্ধারণ করা। কিন্তু দেশটিতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতার ব্যবহারের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি লড়াই শুরু হয়েছে এবং এই লড়াইয়ে ক্ষমতার কাছে গণতন্ত্র হেরে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার শাসনামলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেন এবং করছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হলো—প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা, স্বাধীনভাবে কাজ করে ফেডারেল রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার কমানোর চেষ্টা এবং ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য রিপাবলিকান দল নিয়ন্ত্রিত রাজ্য টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ায় কংগ্রেসের আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়েও রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত আগস্ট মাসে রয়টার্স/ইপসোস পরিচালিত এক জনমত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি মার্কিন নাগরিক মনে করেন, দলীয় স্বার্থে আসনের সীমানা পরিবর্তন করা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।
যে দল যে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকে, তারা আইনসভায় তাদের আসন বাড়ানোর জন্য এমনভাবে সীমানা পুনর্বিন্যাস করে, যেন খুব সহজেই তাদের প্রার্থী ওই আসনে বিজয়ী হতে পারেন। এখানে সাধারণ ভোটারদের পছন্দ-অপছন্দের খুব একটা ভূমিকা থাকে না, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির জন্য ক্ষতিকর। রিপাবলিকানদের আসন পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগের পর ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোর নেতারা বলেছেন, রিপাবলিকানরা এমন কাজ করলে তারাও একই ধরনের পদক্ষেপ নেবেন। দু-দলের এই পাল্টাপাল্টি অবস্থান দেশটির দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। রিপাবলিকান জনমত জরিপকারী হুইট আয়রেসের মতে, গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে, ভিন্নমতের মানুষের মতপ্রকাশ করতে দেওয়া। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন সেই সুযোগ কমছে।
২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতবেন—এ কথা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। বরং আমি তার পরাজয়ের পক্ষে আমার সব সম্পদ বাজি ধরতেও রাজি ছিলাম। কারণ তিনি কোনো রাজনীতিবিদ নন, একজন ব্যবসায়ী। আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিযোগিতা রাজনীতিবিদদের মধ্যেই হওয়া উচিত। কারণ আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক রাজনীতিবিদ রয়েছেন। সংগত কারণেই রাজনীতির বাইরের কোনো লোকের বা একজন বহিরাগতের পক্ষে কোনো নির্বাচনে সফল হওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকানরা সুশিক্ষিত এবং পরিণত নাগরিক। তাদের পক্ষে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সম্ভাবনা কম এবং ট্রাম্পের উসকানিমূলক ব্যক্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার তাকে ভোট দেবেন না বলেই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমার ধারণা, ভুল প্রমাণ করে ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছিলেন। এটা ছিল আমার জন্য একটি বড় শিক্ষা। এই নির্বাচনের পর আমি আমার ধারণার পুনর্মূল্যায়ন করি, যা আমাকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করেছিল।
নাগরিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে যেসব কারণ প্রভাবিত করে, সেগুলো একত্র করে নির্বাচন, যেখানে ক্ষমতা মার্কিনিদের জীবনের একটি প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ট্রাম্পের দক্ষতা তার রাজনৈতিক অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতাকে ঢেকে দিয়েছিল। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্কিন জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোককে নিজের পক্ষে টানার বা তাদের সমর্থন আদায় করার গুণাবলি ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের ছিল না। ফলে রিপাবলিকানদের জন্য এই নির্বাচনে বিজয় উদযাপন করা সহজ হয়েছে।
অন্যান্য সমাজের মতো সম্ভবত আমেরিকান সমাজও দুটি সমান্তরাল বাস্তবতা রয়েছে। এর একটি হচ্ছে, যা আদর্শ, যা একটি জাতির উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে, যা নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন দ্বারা সমর্থিত। এর বিপরীতে, সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধারণাকে ছোট করে দেখে। এই অংশটি মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র মূলত একটি ক্ষমতার দিকে ধাবিত জাতি। কাজেই নিজের পরাশক্তির অবস্থানের বাস্তবতার আলোকেই এই রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া উচিত। আর ক্ষমতার কারণে প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে সহিংসতার উপাদান জড়িত থাকে।
এটা স্পষ্ট, ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বিপরীতে একজন ‘শক্তিশালী’ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের এই ব্যর্থতা ট্রাম্পকে সেই শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে আরো শক্তিশালী করেছে, যা অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেন। সাম্প্রতিক জরিপগুলোর ফলে এটি স্পষ্ট হয়েছে, বেশির ভাগ ভোটার মনে করেন, ট্রাম্প তার সাংবিধানিক কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করছেন। কিন্তু তারপরও এটি আমেরিকান জাতিকে মেনে নিতে হবে যে, তার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয়েছে।
অবশেষে, আমি বুঝতে পারলাম যে, কয়েক দশক ধরে আমেরিকা সম্পর্কে আমার যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক নয়। এটি সেসব মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে যারা তথ্যগুলো বিকৃত করে মানুষের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা রাখে। এসব মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠান প্রায়ই এমনভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরে, যা বিষয়টিকে প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিবর্তে তাদের ‘করপোরেট মিশন’ হিসেবে তুলে ধরে। এই প্রক্রিয়ার প্রতি অসংখ্য প্রভাবশালী লেখকেরও সমর্থন রয়েছে, যারা সামাজিক চিন্তাভাবনা এবং মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।
যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবারিত, এমনকি যখন এর সঙ্গে উসকানি বা অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা যুক্ত হয়, তখন তা দেশটিতে সহিংসতা বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ জনের জন্য গড়ে ১২০টি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইন্সে দেওয়া হয়, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। এই অস্ত্র একজন মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সংঘাতের সময় সহজেই সহিংস কর্মকাণ্ডকে উসকে দিতে পারে। ক্ষুব্ধ নাগরিকদের একটি ছোট অংশ ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নানা অপরাধ সংঘটিত করতে পারে, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ চার্লস কার্কের হত্যাকাণ্ড। সাধারণ নাগরিকদের হাতে বন্দুকের এই ছড়াছড়ি ক্ষমতাতাড়িত প্রেসিডেন্টকে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে নিজের শক্তি প্রদর্শনে উৎসাহিত করে।
প্রকৃতপক্ষে, ট্রাম্প হলেন মার্কিন নাগরিকদের গণতন্ত্রের বিনিময়ে ক্ষমতায় আসা একজন প্রেসিডেন্ট, যাকে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। যদিও তিনি সামরিক সংঘাত এড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি তিনি রক্ষা করছেন না। তিনি ইসরাইলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইরানে হামলা করেছেন এবং মার্কিন বাহিনী ক্যারিবীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় সন্দেহভাজন মাদক চোরাকারবারিদের জাহাজগুলোয় হামলা করছে। এগুলো ট্রাম্পের অবৈধ সহিংস কর্মকাণ্ডের উদাহরণ, যা তার সমর্থকদের মধ্যে তার ক্ষমতার মর্যাদাকে শক্তিশালী করে।
এদিকে, ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারী নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশেই ‘নো কিংস’ আন্দোলন নামে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। জোরালো প্রতিবাদ করছেন সাধারণ নাগরিকরা, যা দেশটির ‘সফট ডেমোক্রেসি’র উদাহরণ। সমাজের ‘ক্ষমতাশালী অংশ’ এই বিক্ষোভের কারণে বিরক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। বিক্ষোভকারীরা মনে করেন, ক্ষমতার দাপট নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের যা প্রয়োজন তা হলো গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট নিয়মনীতি এবং জনশৃঙ্খলা।
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্ষমতার ব্যাপক প্রয়োগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার দাপট আগে থেকেই ছিল, এখনো আছে। বর্তমানে মার্কিন সামরিক ব্যয় জিডিপির প্রায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। কিন্তু এই ব্যয় কোনো নির্দিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না। বরং, এর লক্ষ্য হলো পূর্ববর্তী সরকারগুলো গণতন্ত্রকে উন্নত করার নামে প্রতিরক্ষা খাতে যে অবাস্তব ছোট বাজেট ব্যবহার করেছিল, তার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তির মর্যাদা বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্র তার গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলো সঠিকভাবে মেনে চলে না, বরং ক্ষমতাই দেশটির আসল চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের আসল চরিত্রকেই তুলে ধরে।
মডার্ন ডিপ্লোমেসি থেকে ভাষান্তর :
মোতালেব জামালী
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


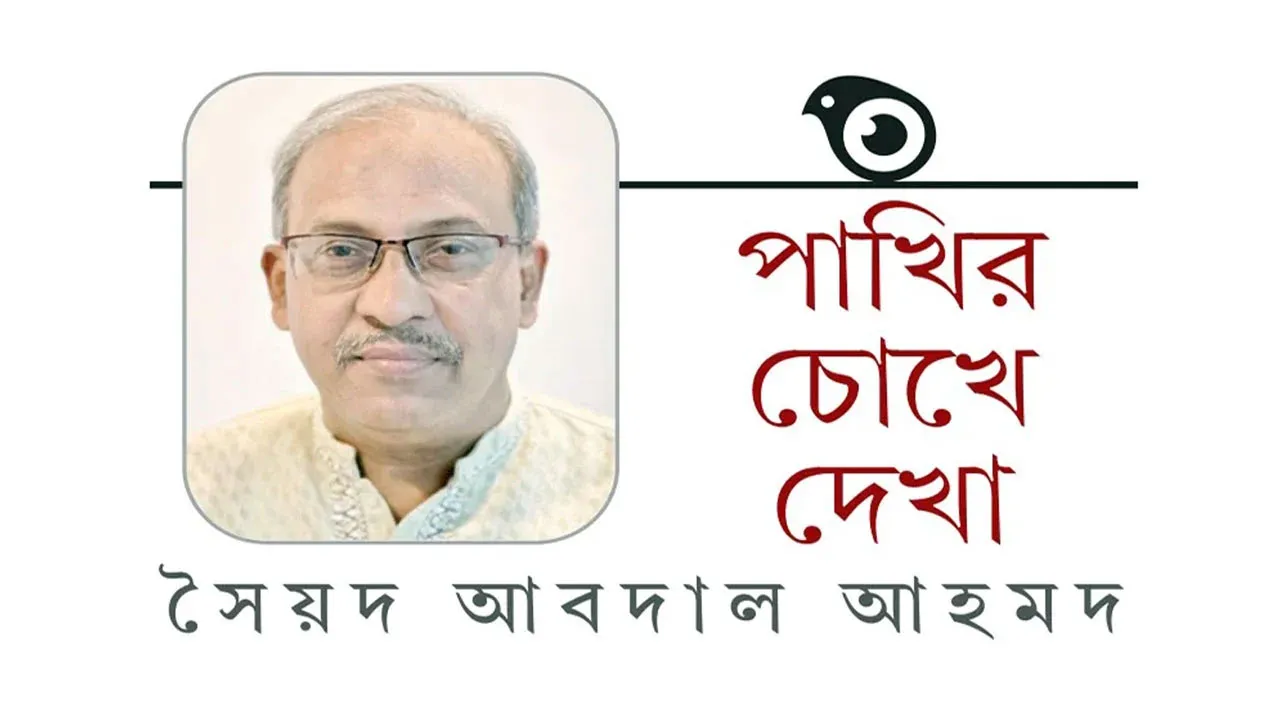 শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতার বিচার
শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতার বিচার নির্বাচনে পতিত ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র
নির্বাচনে পতিত ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র